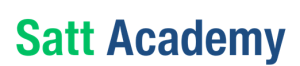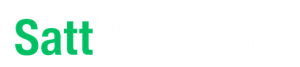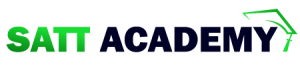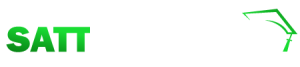হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ চিন্তা করেছে কীভাবে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমাজে এ বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। তবে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী এখন একটি তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। এ তত্ত্বে বলা হয় যে, মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই মহাবিশ্বের একটি গ্রহ পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরের দিকটি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সহজে বোঝা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায় ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত -এ ধরনের ঘটনা থেকে।
এই অধ্যায় শেষে আমরা
- পৃথিবীর উৎপত্তির ঘটনা বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
মলি শুয়ে থাকা অবস্থায় কিছুটা কম্পন অনুভব করল। সে তার ঘরের আসবাবপত্রকেও কিছুটা কাঁপতে দেখল। কম্পনের এ ঘটনাটি একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।
তোমরা জান, আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে বাস করি। আমরা উপরের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? দিনের বেলায় দেখি সূর্য। কখনও দেখি মেঘ। মেঘ না থাকলে রাতের আকাশে দেখি চাঁদ, নক্ষত্র বা তারা। কখনও কী প্রশ্ন জেগেছে মনে, এই পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো? সূর্য, তারা, চাঁদ এরা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

বিভিন্ন সমাজে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। যেমন প্রাচীন চীনের রূপকথায় বলা হয় যে, একটি বিশাল ডিম থেকে প্রথমে একটি দৈত্য জন্ম নেয়। সেই দৈত্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর জন্ম। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ ব্যবহার করে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, প্রায় ১৩৭০ কোটি বা ১৩.৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্ব একটি অসীম ঘনত্বের ও প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিন্দুভরে ঘনীভূত ছিল যা বিস্ফোরিত হয়ে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ বিস্ফোরণকে মহাবিস্ফোরণ বলা হয়। মহাবিস্ফোরণের পর অতি ক্ষুদ্র পদার্থ কণা তৈরি হয়। তারপর ছোট ছোট কণাগুলো কিছুটা ঠান্ডা ও একত্রিত হয়ে জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়। এভাবে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। একদিকে তখন ছোটো ছোটো কণা মিলে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্ছিল। একই সাথে তখন মহাবিশ্ব আরও সম্প্রসারিত হচ্ছিল।

মহাবিশ্বের সকল শক্তি, পদার্থ, মহাকাশ সব কিছু এই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হয় সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন সূর্য যে ধূলিকণা ও গ্যাস থেকে তৈরি হয়েছিল তার কিছু অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তারপর এখন থেকে প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছর পূবে এই ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।
মহাবিস্ফোরণের সমর্থনে প্রমাণ: মহাবিশ্ব একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তার পক্ষে অনেক
তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। এর একটি প্রমাণ হলো, মহাবিশ্ব এখনও বিস্তৃত বা সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাকাশের গ্যালাক্সি/ ছায়াপথ ও তারাসমূহ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই ধারণা করা হয় যে সুদূর অতীতে এরা হয়তো একসময় একসাথে ক্ষুদ্র একটি জায়গায় ছিল; বিস্ফোরণের মাধ্যমে এরা আলাদা হয়েছে।
তোমরা জেনেছ, আমরা যে সৌরজগতে বসবাস করি তা মিল্কিওয়ে (milky way) বা আকাশ গঙ্গা ছায়াপথের অংশ। আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের একটি নক্ষত্র সূর্য। এটি একটি নক্ষত্র কারণ এর নিজের আলো আছে। সূর্য আসলে গ্যাসের একটি পিও। এই গ্যাসের পিণ্ডে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মহাকর্ষ বলের সাহায্যে একত্র হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় প্রচুর তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এরপর সেই তাপ ও আলো সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
সূর্য অনেক পরিমাণে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। তা থেকে কিছু পরিমাণ তাপ ও আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।
সূর্যকে কেন্দ্র করে মহাজাগতিক বস্তু ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল মহাজাগতিক বস্তু ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তু বা জ্যোতিষ্ক।
সূর্যকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে ঘুরছে আটটি গ্রহ। পৃথিবী এমনই একটি গ্রহ। পৃথিবীর আকৃতি গোলকের মতো। পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের মতো তাপ ও আলো উৎপাদন করতে পারে না। তাই আলো ও তাপের জন্য পৃথিবী সূর্যের উপর নির্ভর করে। সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদের তৈরি খাদ্যের উপর নির্ভর করে প্রাণীরা বেঁচে আছে। সূর্য থেকে তাপ আসে বলে পৃথিবী খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। এভাবে সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে জীবদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।
আমাদের পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। চাঁদ নিজে তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। তাহলে চাঁদকে আমরা আলোকিত দেখি কেন? আসলে সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি। চাঁদ ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। চাঁদের পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়ো। আকাশে তো সূর্য আর চাঁদকে প্রায় সমানই মনে হয়, তাই না? কেন এমন মনে হয়? সূর্য অনেক দূরে বলে একেও ছোটো দেখায়। আচ্ছা, সূর্য যদি একটা ফুটবলের মতো হয় তাহলে পৃথিবী কতটুকু?

পৃথিবী তাহলে হবে একটা বালুকণার সমান। সূর্যের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ১০৯ গুণ বড়ো। আমরা দেখি পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য উপযোগী স্থান। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে, নক্ষত্রে বা উপগ্রহে কি জীবেরা বাস করে? ছোটো, বড়ো বা যে কোনো ধরনের জীব? বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন যে, অন্য কোথাও জীব আছে কিনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কেন তাহলে শুধু পৃথিবীতেই জীবন আছে? পৃথিবীতে এমন কী আছে যে এখানে জীবেরা বাস করতে পারে?
ধারণা করা হয়, সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে গ্যাসও ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তার লক্ষ লক্ষ বছর পর এই ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। শুরুর দিকে পৃথিবী বেশ গরম ছিল। এত গরম ছিল যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ টগবগ করে ফুটত। জীবনের জন্য যে তরল পানি দরকার তা ছিল না। বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। পৃথিবী এই অবস্থায় থাকলে কোন জীবের উদ্ভব হতো না।
ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি উত্তপ্ত পৃথিবী |
ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে বায়ুমণ্ডল ও তরল পানির সৃষ্টি |
বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি |
প্রবাহচিত্র: পৃথিবীতে জীবের উপযোগী পরিবেশের বিকাশ
ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে তাপ সরে গিয়ে ঠান্ডা হয়েছে। ঠান্ডা হওয়ার সময় ভারি পদার্থগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে। আর হালকা পদার্থগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে রয়ে গেছে। বিভিন্ন গ্যাস যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি বায়ুমণ্ডল গঠন করেছে। এরপর পৃথিবী আরও ঠান্ডা হয়ে জলীয়বাষ্প তরল পানি হয়ে সমুদ্র তৈরি করেছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়েছে। এসব উপাদান জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব উপাদান পৃথিবীতে তৈরি হওয়ায় পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে ও জীব টিকে থাকতে পারছে।
তোমরা জেনেছ সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে। পৃথিবী তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরি করে। একে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। তারপর কিছুটা ভারি পদার্থগুলো তৈরি করেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূপৃষ্ঠ। আর সবচেয়ে ভারি পদার্থগুলো মিলে তৈরি করেছে পৃথিবীর ভেতরের অংশ।
বায়ুমণ্ডল: যে বায়বীয় অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জানো যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলোও পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে।
ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার। এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগ গ্যাস ও মেঘ থাকে। তোমরা জেনেছ যে, মেঘ আসলে জলীয়বাষ্প দিয়ে তৈরি। ট্রপোস্ফিয়ারের ঠিক ওপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এই স্তর ট্রপোস্ফিয়ারের ওপরে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুণী রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে গ্যাসগুলো খুব কম পরিমাণে আছে।
আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর বাস করি। পৃথিবী-পৃষ্ঠের ওপরে বায়ুমণ্ডল আর নিচের দিকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠকে কেমন দেখি? পৃথিবীর পৃষ্ঠের কোন অংশ নরম মাটি, কোন তাংশ শক্ত পাথর আর কোন অংশ পানি দ্বারা আবৃত। পৃথিবী পৃষ্ঠ বা ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখলেই তোমরা বিষয়টি বুঝবে। ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে বিশাল বিশাল সাগর ও মহাসাগর। এছাড়া আছে লেক বা হ্রদ, নদী, খাল-বিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশ। অন্য মহাসাগরগুলো হচ্ছে প্রশান্ত, আটলান্টিক, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর। সাগরের পানিতে প্রচুর মাছসহ নানা জীব বাস করে। সাগরের পানির উপর দিয়ে চলে মালবাহী জাহাজ।
তোমরা জানো যে, বৃষ্টি ও বরফগলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। নদী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?
আসলে বরফ গলা পানি ও বৃষ্টির পানি ঢাল বেয়ে নিচে প্রবাহিত হয়ে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালার চূড়ায় অনেক বরফ জমা আছে। এই বরফগলা পানি যখন পর্বতের গা বেয়ে নেমে আসে তখন সরু নদীর সৃষ্টি হয়। এই সরু নদীর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে নদী বড় হতে থাকে। নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশে বেশ বৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বতমালায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলো এই বৃষ্টির পানি প্রচুর পরিমাণে বহন করে। তাই পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীগুলো বেশ বড়ো।
পৃথিবীর ভেতরের অংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ঘিরে যে শক্ত স্তর রয়েছে তা শিলামণ্ডল। শিলামণ্ডল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। শিলামণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডল আর সবশেষে পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে কেন্দ্রমণ্ডল (চিত্র-১২.৫)। ধারণা করা হয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পর বাইরের অংশ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাপ চলে যাওয়ায় ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের দিক থেকে তাপ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল বেশ উত্তপ্ত।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গোলকাকার জায়গা হলো কেন্দ্রমণ্ডল। কেন্দ্রমণ্ডলে নিকেল, লোহা, সীসা ইত্যাদি ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডলের ভেতরের অংশে এরা কঠিন কিন্তু বাইরের দিকে এরা গলিত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের মাঝে রয়েছে গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডলের বেশির ভাগই কঠিন। কিন্তু এর কিছু অংশ আধা-গলিত অবস্থায় আছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, আগ্নেয়গিরির উদগীরণে এই অংশটি থেকে গলিত লাভা বের হয়ে আসে।
পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নিচে বেশি দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তোমরা বড়ো হয়ে কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল সম্পর্কে আরও জানবে। তোমরা এই শ্রেণিতে কিছুটা জানবে শিলামণ্ডল সম্পর্কে।
মানুষ সবসময়ই জানতে চেয়েছে কেন ভূমিকম্প হয়? জানতে চেয়েছে কেন আগ্নেয়গিরির উদগীরণ হয় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো জায়গা দিয়ে ভীষণ উত্তপ্ত তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে? বিভিন্ন বিজ্ঞানী, বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব নামে একটি তত্ত্ব নিয়ে আসেন। এই তত্ত্ব দ্বারা ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এ তত্ত্ব সকলের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।
প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব: এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো, ভূপৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর শিলামণ্ডল কতগুলো অংশে
বা খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোকে প্লেট বলা হয়। এই প্লেটগুলো গুরুমণ্ডলের আংশিক তরল অংশের উপরে ভাসমান অবস্থায় আছে। এই প্লেটগুলো প্রতিবছরে কোনো একদিকে কয়েক সেন্টিমিটার সরে যায়। প্লেটগুলো কখনো একটি থেকে আরেকটি দূরে সরে যায়। আবার কখনো কখনো একে অন্যের দিকে আসে। কখনো কখনো প্লেটগুলো বছরে কয়েক মিলিমিটার উপরে ওঠে বা নিচে নামে। একটি প্লেটের সাথে আরেকটি প্লেট যেখানে মেশে সেখানেই বেশি ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা ঘটে। প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে উঁচু পর্বত থাকলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা আরও বাড়ে।
ধারণা করা হয়, প্লেটগুলো একটি আরেকটির সাথে ঘষা বা ধাক্কা খেলে সেখানে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপে ভূ-অভ্যন্তরের পদার্থ গলে যায়। এ গলিত পদার্থ চাপের ফলে নিচ থেকে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। একেই আগ্নেয়গিরির উদগীরণ বলে। ভূঅভ্যন্তরে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা ম্যাগমা নামে পরিচিত এবং বেরিয়ে আসা গলিত তরল পদার্থকে লাভা বলে। একইভাবে প্লেটগুলো একটি অন্যটির সাথে ধাক্কা খেলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। একেই ভূমিকম্প বলে। আজকাল বাংলাদেশেও ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে।

শিলামণ্ডলের উপরের দিকের অংশ ভূত্বক নামে পরিচিত। ভূত্বক হয় পানি নয়ত মাটি দ্বারা আবৃত। ভূত্বকের বেশির ভাগ পানি দ্বারা আবৃত। বাকি অংশটি গুড়ো বা ভাঙা পাথুরে পদার্থ দ্বারা আবৃত। এ মাটি সাধারণত জৈবপদার্থ দ্বারা গঠিত ও নরম হয় তাহলে তাকে মাটি বলা হয়। ভূত্বক মানুষের জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশের উপরে আমরা বসবাস করি। মাটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করি। এছাড়াও এ অংশে রয়েছে খনিজ পদার্থ যা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।
মাটি গঠন প্রক্রিয়া: সাধারণত পাথর, নুড়ি, কাঁকর, বালি, কাদা ইত্যাদি দ্বারা ভুত্বক গঠিত। এদের সাথে মিশে থাকে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের অংশ। ভূত্বক গঠনকারী এসকল কঠিন পদার্থের সাধারণ নাম শিলা। কঠিন শিলা থেকে নরম মাটি তৈরি হয় সাধারণত দু'টি পর্যায়ে:
১. প্রথম পর্যায়: কঠিন শিলা দীর্ঘদিন ধরে রোদ, বৃষ্টি, বঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। এছাড়া বায়ু, বরফ বা পানির প্রবাহ ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে অন্য জায়গা থেকে ক্ষুদ্র শিলাকণা এসে একটি স্থানে জমা হয়।
২. দ্বিতীয় পর্যায়: ক্ষুদ্র শিলাকণার সাথে পানি, বায়ু, ক্ষুদ্র জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ যোগ হয়।
বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানের মাটি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, গঠনেও ভিন্ন। তবে মাটির উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে অনুসন্ধান করলে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি মাটির একদম উপরের স্তরটিতে পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে থাকে। পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে তৈরি কালো বা অনুজ্জ্বল উপাদানকে হিউমাস বলে। মাটির উপরের দিকে হিউমাস বেশি থাকে। এই হিউমাস থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। দ্বিতীয় স্তরে হিউমাস কমে আসে, এ জন্য কম কালো বা কিছুটা উজ্জ্বল হয়। তৃতীয় স্তর মূলত ক্ষুদ্র শিলাকণা দ্বারা গঠিত। সবশেষে নিচের স্তরটি কেবল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।
বাংলাদেশে নদীর কাছাকাছি স্থানে বন্যা হয়। বন্যার পানি পলিমাটি বয়ে আনে। নদীর কাছাকাছি এসব স্থানের মাটির উপরিভাগ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এসব স্থানের মাটির উপরের স্তর সেজন্য খুব পুরনো হয় না। এ মাটি ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী।

খনিজ পদার্থ
আগেই বলা হয়েছে যে, ভূত্বক বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর কিছু অংশ জৈবপদার্থ দিয়ে গড়া। আরও আছে অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশের মধ্যে অনেক সময় একাধিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কখনো একটি অজৈব পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় না থেকে আলাদা থাকে। এরূপ অজৈব পদার্থকে খনিজ পদার্থ বলে। খনিজ পদার্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এদেরকে মানুষ তৈরি করে না, এদেরকে প্রকৃতিতেই পাওয়া যার। চুনাপাথর একটি খনিজ পদার্থ। চুনাপাথর আসলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নামের একটি পদার্থ। বাংলাদেশের জয়পুরহাটে ও সিলেটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর থেকে সিমেন্ট তৈরি হয়। সাধারণত মাটির নিচের দিকে খনিজসম্পদ বেশি পাওয়া যায়। কখনও কখনও এরা উপরের মাটির সাথেও মিশে থাকে। দরকারি অনেক খনিজসম্পদ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। দালান তৈরিতে যে রড ব্যবহার করা হয় তা লোহার তৈরি। গাড়ি, বাস, লঞ্চ এগুলোও তৈরি হয় লোহা থেকে।
টিউবওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক/তারকাঁটা, যন্ত্রপাতি এগুলোও লোহা থেকে তৈরি। লোহা মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু হাঁড়ি-পাতিল, চামচ তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম থেকে। লোহার মতো অলুমিনিয়ামও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। তামা, রুপা, সোনা, দস্তা এসব দরকারি ও দামি পদার্থও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অবশ্য এসব খনিজসম্পদ বেশি পরিমাণে নেই।
কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির নিচে পাওয়া গেলেও এদেরকে খনিজ পদার্থ বলা হয় না। কারণ এরা জীবদেহ থেকে তৈরি, এরা অজৈব নয়। বড়ো বড়ো গাছ মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘ সময়ে এরা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়েছে। জীবদেহ থেকে তৈরি এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। আমাদের দেশে মাটির নিচে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানি হিসেবে বেশ ভালো। এগুলো পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে কলকারখানা চলে, যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রান্না করা হয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যও তৈরি করা হয়। যেমন: প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন তৈরি করা হয়।
এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম
- কোটি কোটি বছর আগে একটি মহাবিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।
- সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে পৃথিবী ও আরও সাতটি গ্রহ। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ হলো চাঁদ।
- সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী খুব গরম ছিল। ধীরে ধীরে এটি ঠাণ্ডা হয়ে জীবের বাসের উপযোগী হয়েছে। পৃথিবীতে পানি ও নানা রকম গ্যাস আছে বলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর তিনটি অংশ- বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠ ও ভেতরের অংশ। বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নানা গ্যাস। ভূপৃষ্ঠ ঢাকা আছে পানি, মাটি ও শিলা দ্বারা।
- বরফগলা পানি ও বৃষ্টির পানি ঢাল বেয়ে নিচে প্রবাহিত হওয়ায় ফলে নদীর সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর ভেতরের অংশ বা অভ্যন্তর আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আছে কেন্দ্রমণ্ডল, মাঝখানে গুরুমণ্ডল আর উপরের দিকে শিলামণ্ডল।
- শিলামণ্ডল কতগুলো প্লেটে বিভক্ত। এই প্লেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়।
- কঠিন শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সাথে পানি, বায়ু, ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ মিলে মাটি তৈরি হয়।
- মাটির নিচে রয়েছে অনেক দরকারি পদার্থ। এদের মধ্যে অজৈব পদার্থকে বলে খনিজ পদার্থ। এছাড়া রয়েছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস, ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি।
Read more